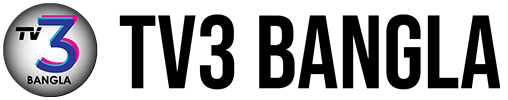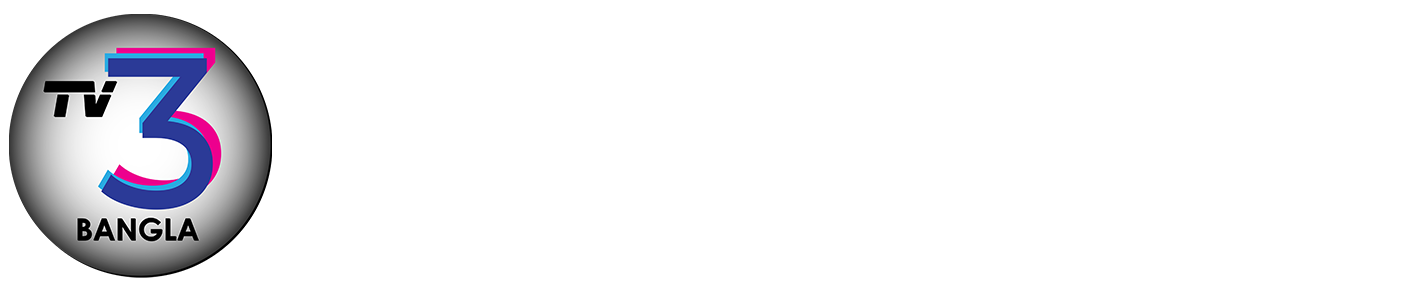জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার বাইগুনি গ্রামে বসে আছেন ৪৫ বছর বয়সী সফিরুদ্দিন। পেটের নিচের অংশে চাপ দিলে এখনো ব্যথা অনুভব করেন। তিন সন্তান ও পরিবারের জন্য একটি ঘর বানাতে ২০২৪ সালে নিজের একটি কিডনি বিক্রি করেন ভারতের এক রোগীর কাছে। দাম পান সাড়ে তিন লাখ টাকা।
কিন্তু সেই টাকায় ঘরের কাজ শেষ হয়নি। অপারেশনের পর শরীরের দুর্বলতা ও ব্যথা তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এখন তিনি একটি হিমাগারে শ্রমিকের কাজ করেন, তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিয়মিত কাজ করতেও পারছেন না।
দালালদের প্ররোচনায় সফিরুদ্দিন ভিসা, ফ্লাইট, হাসপাতালের কাগজসহ সব কিছুতেই সাহায্য পান। তাকে রোগীর আত্মীয় দেখিয়ে ভুয়া আইডি, নকল জন্মসনদ, নোটারি সার্টিফিকেট তৈরি করে ভারতে পাঠানো হয়। কাকে কিডনি দিচ্ছেন—তা-ও জানতেন না তিনি।
ভারতে কিডনি প্রতিস্থাপন আইনত নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই বৈধ। তবে দালাল চক্র ভুয়া আত্মীয়তা ও কাগজপত্র তৈরি করে এই সীমা এড়িয়ে যায়। কেউ কেউ ভুয়া ডিএনএ রিপোর্টও বানায়। এতে জড়িত থাকে দালাল, কাগজপত্র প্রস্তুতকারী, হাসপাতাল কর্মী এমনকি চিকিৎসকেরাও।
বাইগুনি গ্রামের চিত্র ভয়াবহ। ৬ হাজার মানুষের এই গ্রামে এত বেশি মানুষ কিডনি বিক্রি করেছেন যে, গ্রামটির নামই হয়ে গেছে ‘এক কিডনির গ্রাম’। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, কালাই উপজেলায় প্রতি ৩৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন কিডনি বিক্রি করেছেন। বেশিরভাগই দরিদ্র, ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী পুরুষ।
অপারেশনের পর সফিরুদ্দিন তার পাসপোর্ট বা প্রেসক্রিপশন কিছুই ফেরত পাননি। ওষুধও জোটেনি। দালালরা সব কাগজপত্র রেখে দেয় যাতে বিক্রেতারা কোনো দাবি বা অভিযোগ করতে না পারেন। অনেককেই ভারতে ফেলে রেখে আসা হয়।
কিডনিগুলো মূলত বিক্রি হয় ভারতের ধনী রোগীদের কাছে, যারা লাইনে না থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কিডনি নিতে চান। ভারতে বছরে প্রায় ২ লাখ মানুষ শেষ ধাপের কিডনি রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু ২০২৩ সালে মাত্র ১৩,৬০০ জনের প্রতিস্থাপন হয়েছে।
মোহাম্মদ সজল (ছদ্মনাম) ২০২২ সালে কিডনি বিক্রি করেন দিল্লির এক হাসপাতালে। চুক্তি ছিল ১০ লাখ টাকার, কিন্তু পান মাত্র সাড়ে ৩ লাখ। প্রতারিত হওয়ার পর তিনিও এই চক্রে যুক্ত হন। পরে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারণে সে চক্র থেকে বেরিয়ে এসে এখন ঢাকায় রাইড শেয়ারিং ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছেন।
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারতে এসব প্রতিস্থাপন যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো সমন্বিত তথ্য বা ব্যবস্থা নেই। ভারতের হাসপাতালগুলো দায় এড়িয়ে যায়। অথচ অনেক হাসপাতালই জেনে-বুঝেই জাল কাগজ গ্রহণ করে, কারণ এতে তাদের আয় বাড়ে।
ভারতের মেডিকেল ট্যুরিজম শিল্প বছরে ৭.৬ বিলিয়ন ডলারের, যার বড় অংশ জুড়ে বিদেশি রোগীদের অঙ্গপ্রতিস্থাপন। ২০১৯ সালে কিছু ডাক্তার ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সেটি ছিল বিচ্ছিন্ন প্রয়াস।
একজন দালাল মিজানুর রহমান জানান, একটি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টে খরচ হয় প্রায় ২৫ থেকে ৩৫ লাখ টাকা। কিন্তু বিক্রেতা পান মাত্র ৩-৫ লাখ। বাকি টাকা দালাল, কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের পকেটে যায়। কখনও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে ফাঁদে ফেলা হয়।
ভারতের কিডনি ওয়ারিয়ার্স ফাউন্ডেশনের প্রধান বাসুন্ধরা রঘুবংশ বলেন, ‘আইন থাকলেও বাস্তবতা হলো—এটি এক কালোবাজারে পরিণত হয়েছে।’ তার মতে, কিডনি দান বন্ধ করা না গেলেও একটি মানবিক, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি—যেখানে বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও আর্থিক নিরাপত্তা থাকবে।
সূত্রঃ আল জাজিরা
এম.কে
০৪ জুলাই ২০২৫